আমাদের হাতে থাকা মোবাইল ফোন এখন আর কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়—এটি যেন ব্যক্তিগত জীবনের এক ডিজিটাল আর্কাইভ। প্রতিটি কল, বার্তা, অবস্থান কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কাটানো সময়—সবকিছুই আমাদের সম্পর্কে তথ্য বলে দেয়। এই তথ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নাগরিকের গোপনীয়তার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সংবেদনশীল।
বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে নাগরিকের ফোন ও অনলাইন তথ্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। সরকার সাইবার অপরাধ দমন, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে মোবাইল ফোনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এই নিয়ন্ত্রণ কতটা বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত? এবং কীভাবে তা নাগরিকের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ না করেই করা সম্ভব?
আইনি কাঠামো ও নিয়ন্ত্রণের পরিধি
বাংলাদেশ সরকার মোবাইল ফোনের তথ্য নিয়ন্ত্রণ করে মূলত দুটি আইনের আওতায়—
(ক) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) মোবাইল অপারেটরদের লাইসেন্স প্রদান ও তদারক করে। এই আইনের ধারা ৯৭ অনুযায়ী “রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা জনস্বার্থে” সরকার টেলিযোগাযোগ কার্যক্রমে প্রবেশাধিকার বা নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে। অর্থাৎ, আদালত বা অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ফোনকল, মেসেজ বা লোকেশন ট্র্যাক করার ক্ষমতা সরকারের আছে।
(খ) ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (বর্তমানে সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩) অনলাইন অপরাধ ও সাইবার সন্ত্রাস দমনের উদ্দেশ্যে প্রণীত। এই আইনের আওতায় সন্দেহজনক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সরকার বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোবাইল ও অনলাইন তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। যদিও উদ্দেশ্য জননিরাপত্তা রক্ষা, বাস্তবে এর প্রয়োগে নাগরিক স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
মোবাইল তথ্যের ধরন
একটি মোবাইল অপারেটরের হাতে থাকা তথ্য তিন শ্রেণির—
ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ তথ্য (Personal Identifiers): নাম, এনআইডি, ঠিকানা, বায়োমেট্রিক ডেটা ইত্যাদি।
মেটাডেটা (Metadata): কে কাকে কল করেছে, সময়কাল, টাওয়ার লোকেশন ইত্যাদি।
কনটেন্ট ডেটা (Content Data): ফোনালাপ, এসএমএস বা অনলাইন বার্তার আসল বিষয়বস্তু।
২০১৬ সালে সিম নিবন্ধনের সময় বায়োমেট্রিক তথ্য বাধ্যতামূলক করার পর থেকে অপারেটরদের হাতে নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্যের ঘনত্ব বেড়েছে। সাধারণত “ল’ফুল ইন্টারসেপ্ট” প্রক্রিয়ায় সরকার মেটাডেটা ব্যবহার করে তদন্ত চালায়। তবে কনটেন্ট ডেটায় অনুমতি ছাড়া প্রবেশ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী গোপনীয়তার লঙ্ঘন।
সংবিধান ও গোপনীয়তার অধিকার
বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদ নাগরিককে “ব্যক্তিগত যোগাযোগের গোপনীয়তা ও গৃহের স্বাধীনতা” নিশ্চিত করেছে। অর্থাৎ আদালতের অনুমতি ছাড়া ফোনালাপ বা বার্তা তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপমুক্ত থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে এই সীমা প্রায়ই লঙ্ঘিত হয়।
জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন (UNHRC, ২০১৩) বলেছে, “নজরদারি তখনই বৈধ, যখন তা প্রয়োজনীয়, অনুপাতিক এবং বিচারিকভাবে অনুমোদিত।” বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই মানদণ্ড এখনো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
ভারসাম্য আনার উপায়
গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য আনতে কিছু পদক্ষেপ জরুরি—
-
বিচারিক অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা: ফোনের তথ্য সংগ্রহের আগে আদালতের লিখিত অনুমতি নেওয়া।
-
স্বচ্ছতা রিপোর্ট প্রকাশ: বিটিআরসি ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রতিবছর নজরদারির সংখ্যা ও অনুমোদনের পরিসংখ্যান প্রকাশ করবে।
-
তথ্য সংরক্ষণ সীমিতকরণ: অপারেটররা অপ্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করবে না; নির্দিষ্ট সময় পর তা মুছে ফেলবে।
-
গোপনীয়তা কমিশন গঠন: একটি স্বাধীন কমিশন নাগরিকের অভিযোগ তদন্ত ও তদারকি করবে।
-
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন ও সচেতনতা: নাগরিককে নিজের তথ্য ব্যবহারে সচেতন হতে হবে।
আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা
ইউরোপীয় ইউনিয়নের General Data Protection Regulation (GDPR, ২০১৮) আইন অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ কেবল “প্রয়োজনীয়তার সীমায়” করা যায় এবং নাগরিককে তা জানাতে হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) অনুযায়ী আদালতের অনুমতি ছাড়া ফোন বা ইন্টারনেট তথ্য ইন্টারসেপ্ট করা নিষিদ্ধ।
কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় স্বাধীন Privacy Commissioner অফিস সরকারি নজরদারি তদারকি করে।
বাংলাদেশে এখনো এমন স্বাধীন তদারকি কাঠামো নেই।
ডিজিটাল যুগে গোপনীয়তা হারানো মানে কেবল ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস নয়; এর অর্থ নাগরিক স্বাধীনতা সংকুচিত হওয়া। অতিরিক্ত নজরদারি মানুষকে ‘self-censorship’-এর দিকে ঠেলে দেয়। আর রাষ্ট্র যখন নাগরিকের সব ডেটা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে, তখন অপব্যবহারের আশঙ্কা বাড়ে।
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা যেমন জরুরি, তেমনি নাগরিকের গোপনীয়তা রক্ষা করাও সাংবিধানিক দায়। তাই নজরদারি হতে হবে সীমিত, স্বচ্ছ ও বিচারিক তদারকিপূর্ণ। রাষ্ট্র যখন নাগরিকের ডেটায় প্রবেশের চাবি ধরে রাখে, তখন তার জবাবদিহিতার তালাটিও নাগরিকের হাতে থাকা জরুরি।

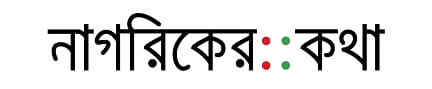







No comments yet. Be the first to comment!