তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে ইন্টারনেট আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। ব্যাংকিং, কেনাকাটা, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবা—সব ক্ষেত্রেই আমরা অনলাইন নির্ভর হয়ে পড়েছি। কিন্তু এই নির্ভরতার সঙ্গে বেড়েছে আরেকটি ভয়াবহ ঝুঁকি—ব্যক্তিগত তথ্য চুরি ও তথ্যের অপব্যবহার।
আমরা যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি দিই, কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করি বা অনলাইন লেনদেন করি, তখন অজান্তেই নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর এমনকি ব্যাংক তথ্যও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিই। হ্যাকাররা এই তথ্য ব্যবহার করে আর্থিক প্রতারণা, পরিচয় চুরি বা অনলাইন ব্ল্যাকমেইলের মতো অপরাধ ঘটায়।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, প্রতি বছর বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ সাইবার হামলার শিকার হয়। তাই ডিজিটাল যুগে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা এখন বিলাসিতা নয়, বরং জরুরি প্রয়োজন।
ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষায় কিছু সহজ পদক্ষেপ
১️ সচেতনতা ও শক্তিশালী পাসওয়ার্ড:
তথ্য সুরক্ষার প্রথম ধাপ হলো সচেতনতা। অনেকেই দুর্বল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেন, যা সহজে অনুমানযোগ্য। একটি ভালো পাসওয়ার্ডে বড়–ছোট হরফ, সংখ্যা ও বিশেষ চিহ্ন থাকা উচিত—যেমন P@ssw0rd2K25!। প্রতিটি অ্যাকাউন্টে আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন এবং প্রয়োজনে LastPass বা Bitwarden-এর মতো পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার করুন।
২️ টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (2FA):
গুগল, ফেসবুক বা ব্যাংক অ্যাপে এই সুবিধা চালু রাখুন। এতে কেউ পাসওয়ার্ড জানলেও আপনার ফোনে পাঠানো কোড ছাড়া প্রবেশ করা সম্ভব নয়।
৩️ ফিশিং প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকুন:
অচেনা ইমেইল বা মেসেজে পাঠানো লিংকে ক্লিক করবেন না—বিশেষ করে ব্যাংক বা লটারির নামে পাঠানো বার্তায়। প্রয়োজন হলে সরাসরি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে যাচাই করুন।
৪️ সোশ্যাল মিডিয়ার প্রাইভেসি সেটিংস পরীক্ষা করুন:
আপনার পোস্ট কে দেখতে পাবে তা নির্ধারণ করুন। প্রয়োজন ছাড়া ফোন নম্বর, ঠিকানা বা ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকুন।
৫️ প্রযুক্তিগত সুরক্ষা:
অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার (যেমন Avast, Norton) ব্যবহার করুন, নিয়মিত আপডেট দিন। পাবলিক ওয়াই–ফাই ব্যবহার করলে VPN (যেমন ExpressVPN) দিয়ে সংযোগ নিন। শিশুদের ক্ষেত্রে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল টুলস ব্যবহার করুন।
উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতা
ইউরোপীয় ইউনিয়ন:
২০১৮ সালে চালু হওয়া General Data Protection Regulation (GDPR) অনুযায়ী, কোনো কোম্পানি নাগরিকের তথ্য সংগ্রহ করলে অবশ্যই তার সম্মতি নিতে হবে এবং তথ্য ফাঁস হলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে হবে। এই আইনের কারণে ফেসবুকসহ অনেক প্রতিষ্ঠানকে মিলিয়ন ইউরো জরিমানা গুনতে হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র:
একক কোনো জাতীয় আইন না থাকলেও খাতভিত্তিক আইন রয়েছে—যেমন স্বাস্থ্য খাতে HIPAA, শিশুদের সুরক্ষায় COPPA, আর ক্যালিফোর্নিয়ায় CCPA। বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো এখন ব্যবহারকারীর ডেটা বিক্রির আগে অনুমতি নিতে বাধ্য এবং ব্যবহারকারীর “Opt out” অধিকার রয়েছে। অ্যাপল App Tracking Transparency চালু করে ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়া ট্র্যাকিং বন্ধ করেছে।
কানাডা ও জাপান:
কানাডার PIPEDA ও জাপানের APPI আইন অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠান নাগরিকের অনুমতি ছাড়া তার তথ্য ব্যবহার করতে পারে না। তথ্য ফাঁস হলে তা অবিলম্বে জানাতে হয়।
অস্ট্রেলিয়া:
Privacy Act 1988 এবং Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) নাগরিকের তথ্য সুরক্ষায় নজরদারি করে।
এই দেশগুলোয় শুধু আইন নয়, শিক্ষা ও প্রযুক্তিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্কুল পর্যায় থেকেই অনলাইন নিরাপত্তা শিক্ষা চালু আছে।
🇧🇩 বাংলাদেশের বাস্তবতা
বাংলাদেশে এখনো স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র Data Protection Act কার্যকর হয়নি। বিদ্যমান সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ মূলত অপরাধ দমনকেন্দ্রিক; নাগরিকের ডেটা সুরক্ষায় নয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ব্যবহারে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। অনেক সময় নাগরিক জানেন না, তার তথ্য কোথায় ও কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
অন্যদিকে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের প্রবণতা সাইবার অপরাধীদের সুযোগ করে দেয়। অনলাইন লেনদেনে অপরীক্ষিত ওয়েবসাইটে কার্ড তথ্য দেওয়া প্রতারণার ঝুঁকি বাড়ায়। তাই ব্যক্তিগত সচেতনতা ও ডিজিটাল শিক্ষা আমাদের প্রথম প্রতিরক্ষা।

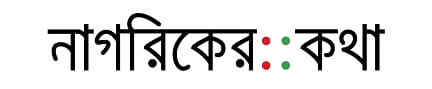







No comments yet. Be the first to comment!